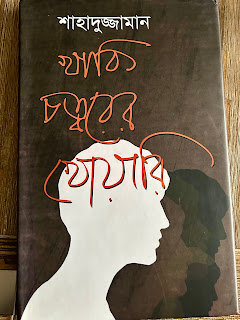চতুষ্কোণ | মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই বইটা আগে পড়া ছিল না। বাতিঘরের ধ্রুপদী সংস্করণের বইটা দেশ থেকে আনিয়েছে তিথি, সেটা হাতে নিয়ে দেখতে গিয়ে এত ভালো লাগছিল যে এক ছুটির দিনের সকাল থেকে সন্ধ্যা টানা পড়ে শেষ করে ফেললাম। পড়তে গিয়ে চট করে 'স্ট্রিম অব কনশাসনেস' টার্মটা মাথায় এলো। মানিকের নিজের লেখায়ও আগে এর ব্যবহার দেখেছি, তবে এত স্পষ্ট করে আগে কখনও চোখে পড়েছে বলে মনে পড়ছে না। গল্পের মূল চরিত্র রাজকুমার, কেন জানি সৈয়দ হকের বাবর আলীকে মনে করিয়ে দেয়। বিষয় হিসেবে রাজকুমারের ভাবনা সেই সময়ে যথেষ্ঠ বিতর্ক তৈরি করার কথা। সত্যিই করেছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে কখনও।